 এই বইটি এবারের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছিলো,,,,,নিয়ে নিন একদম ফ্রীতে,,,,
Download/ডাউনলোড
এই বইটি এবারের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছিলো,,,,,নিয়ে নিন একদম ফ্রীতে,,,,
Download/ডাউনলোড
জাফর ইকবালের নতুন বই- আরো টুনটুনি ও আরো ছুট্টাচ্চু ২০১৫
 এই বইটি এবারের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছিলো,,,,,নিয়ে নিন একদম ফ্রীতে,,,,
Download/ডাউনলোড
এই বইটি এবারের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছিলো,,,,,নিয়ে নিন একদম ফ্রীতে,,,,
Download/ডাউনলোড
 এই বইটি এবারের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছিলো,,,,,নিয়ে নিন একদম ফ্রীতে,,,,
Download/ডাউনলোড
এই বইটি এবারের বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছিলো,,,,,নিয়ে নিন একদম ফ্রীতে,,,,
Download/ডাউনলোড
তুমি যদি ইতিমধ্যে এই বইটি
পড়ে ফেলো এবং এবারে
ভালোভাবে সি শিখতে
চাও, তবে Herbert Schildt-এর
Teach Yourself C বইটি পড়তে
পারো। আবার Brian Kernighan
ও Dennis Ritchie-এর লেখা The
C Programming Language বইটিও
পড়তে পারো। লেখকদের
একজন, Dennis Ritchie, সি
ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজাইন
করেছেন। আর কেউ যদি
তোমার কাছে জানতে চায়
শুরুতে সি শিখতে হলে কোন
ইংরেজি বইটি ভালো তবে
Stephen G. Kochan-এর
Programming in C বইটির কথা
বলে দেবে। এটি সি শেখার
জন্য চমৎকার ও সহজ একটি বই।
Schaums Outlines সিরিজের
Programming with C বইটিও
ভালো। বইতে প্রচুর উদাহরণ
আর অনুশীলনী আছে।
সি শেখার পরে তুমি সি
প্লাস প্লাস বা জাভা
শিখতে পারো। সি প্লাস
প্লাস শেখার জন্য ভালো বই
হচ্ছে Teach Yourself C++
(লেখক: Herbert Schildt) আর
জাভার জন্য Java How to
Program (লেখক: Paul Deitel and
Harvey Deitel)। তারপর অন্য
ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে গেলে
আর বই কেনার দরকার নেই।
ইন্টারনেটে প্রচুর
টিউটোরিয়াল আছে।
সেগুলো পড়ে শিখে
ফেলবে।
সি এবং পাইথনের জন্য
চমৎকার দুটি বই আছে
অনলাইনে -
http://learnpythonthehardway.org/
book/
http://c.learncodethehardway.org/
book/
তুমি যদি কম্পিউটার
বিজ্ঞানে পড়তে চাও,
কিংবা প্রোগ্রামিং
কন্টেস্টে ভালো করতে
চাও, তাহলে তোমার Discrete
Mathematics ভালো করে
শিখতে হবে। এর জন্য Kenneth
H. Rosen-এর Discrete Mathematics
বইটি খুব ভালো।
আগাগোড়া পড়ে ফেলবে।
সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলনীর
সমস্যাগুলো সমাধানের
চেষ্টা করবে। Discrete
Mathematics শেখার পরে
শিখতে হবে অ্যালগরিদম।
অ্যালগরিদম শেখার শুরু আছে
কিন্তু শেষ নেই। আর শুরু করার
জন্য তোমরা পড়তে পারো
Introduction to Algorithms (লেখক:
Thomas H. Cormen, Charles E.
Leiserson, Ronald L. Rivest and
Clifford Stein) এটি
অ্যালগরিদমের মৌলিক
বিষয়গুলো শেখার জন্য আমার
দেখা সবচেয়ে ভালো বই।
প্রোগ্রামিং
প্রতিযোগিতার জন্য কিছু
লিংক:
http://projecteuler.net/
এখানে অনেক মজার সমস্যা
আছে যেগুলোর বেশিরভাগই
প্রোগ্রাম লিখে সমাধান
করতে হয়। এখানে প্রোগ্রাম
জমা দেওয়া লাগে না,
কেবল প্রোগ্রাম দিয়ে বের
করা উত্তরটা জমা দিতে হয়।
http://www.spoj.pl/ এখানেও
অনেক ভালো সমস্যা আছে।
সমাধান করে প্রোগ্রাম জমা
দিলে প্রোগ্রাম সঠিক
হয়েছে কি না তা জানা
যায়। এই ওয়েবসাইটের একটি
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সি, সি
প্লাস প্লাস, জাভা, পার্ল,
পাইথন, রুবি, পিএইচপি
ইত্যাদি ব্যবহার করে
প্রোগ্রাম লেখা যায়।
http://uva.onlinejudge.org/ এই
সাইটে নিয়মিত অনলাইন
প্রোগ্রামিং
প্রতিযোগিতার আয়োজন
করা হয়। এ ছাড়াও
অনুশীলনের জন্য প্রচুর সমস্যা
দেওয়া আছে। নতুন
প্রোগ্রামারদের জন্য এটি
বেশ ভালো জায়গা।
http://ace.delos.com/usacogate
এটি যদিও আমেরিকার
ইনফরমেটিক্স অলিম্পিয়াড
ট্রেনিং প্রোগ্রাম, কিন্তু
সাইটে যেকোনো দেশের
প্রোগ্রামাররাই
রেজিস্ট্রেশন করে অনুশীলন
করতে পারে। তোমরা যারা
প্রোগ্রামিং
প্রতিযোগিতায় ভালো
করতে চাও, তাদের অবশ্যই
এখানে অনুশীলন করা উচিত।
http://www.topcoder.com/tc
এখানেও নিয়মিত অনলাইন
প্রোগ্রামিং
প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
এখানে ভালো ফলাফল
করলে আবার টাকাও দেয়
(কী আনন্দ!)। এ ছাড়া এখানে
অনেক ভালো
টিউটোরিয়াল ও আর্টিকেল
আছে। এটি অভিজ্ঞ
প্রোগ্রামারদের জন্য বেশ
ভালো একটি সাইট।
http://codeforces.com এই
সাইটে নিয়মিত বিভিন্ন
ধরনের প্রোগ্রামিং
কন্টেস্ট হয়। অভিজ্ঞ
প্রোগ্রামারদের জন্য
ভালো।
http://www.codechef.com
এটিও প্রোগ্রামিং
প্রতিযোগিতার জন্য একটি
ভালো ওয়েবসাইট এবং
অভিজ্ঞ প্রোগ্রামারদের
জন্য।
http://ioinformatics.org
আন্তর্জাতিক ইনফরমেটিক্স
অলিম্পিয়াডের
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।
http://cm.baylor.edu/
welcome.icpc এসিএম
আইসিপিসির অফিসিয়াল
ওয়েবসাইট।
প্রোগ্রামিং ছাড়াও
বিজ্ঞান ও গণিতের নানা
বিষয়ের জন্য এই ফোরামে
অংশগ্রহণ করতে পারো:
http://matholympiad.org.bd/
forum/ ।
বাংলা ভাষায়
প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত
কোর্স অনলাইনে করার
ব্যবস্থা করছে দ্বিমিক
কম্পিউটিং স্কুল । সেখানে
প্রোগ্রামিংয়ে
হাতেখড়ি , ওয়েব কনসেপ্টস ও
ডিসক্রিট ম্যাথের উপর
কোর্স রয়েছে।
আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
ওয়েবসাইট হচ্ছে
www.google.com । এটি আসলে
একটি সার্চ ইঞ্জিন। যখনই
কোন কিছু জানতে ইচ্ছা
করবে, google-এ সার্চ করলে
তুমি সেই বিষয়ের নানা
তথ্যসমৃদ্ধ ওয়েবসাইটের
লিংক পেয়ে যাবে।
“কন আর্টিস্ট” নামটার সাথে
আমরা অনেকেই কম বেশী
পরিচিত। সোজা বাংলায়
বললে প্রতারক। হলিউডের
সিনেমা “Ocean Eleven”
কিংবা বলিউডের “ধুম”
দেখে কি কেও কখনো
চিন্তা করেছেন বাস্তবে এই
রকম ঘটনা ঘটেছে কিনা।
সম্ভবত কেও চিন্তাও করেননি
বাস্তব জীবনেও রয়েছেন এমন
কিছু মানুষ আর তাদের
কুকীর্তি সিনেমাকেও
ছাড়িয়ে যায়। আসুন পরিচিত
হয় “কন আর্টিস্ট” দের দুনিয়ার
কিছু রথী মহারথীদের সাথে।
শুরুতেই যার নাম আসবে তিনি
হলেন জর্জ ম্যাকগ্রেগর।
জাতিতে স্কটিশ এই লোকের
জন্ম ২৪ ডিসেম্বর ১৭৮৬। ১৬ বছর
বয়সেই যোগ দেন ব্রিটিশ
সেনাবাহিনীতে । দ্রুত
পদোন্নতি ও হয়। কিন্তু উচ্চপদস্ত
কিছু কর্মকর্তার সাথে
বিরোধে জড়িয়ে বেরিয়ে
আসেন সেনাবাহিনী
থেকে। ততদিনে সাউথ
আমেরিকার স্বাধীনতার
আন্দোলনের অনেক খবর জেনে
গেছেন। ইয়োরোপীয় দখলদার
থেকে মুক্তির জন্য লড়ছে
সাউথ আমেরিকানরা। তিনি
ও সুযোগের সন্ধানে পাড়ি
দিলেন সেখানে। তারপর
কখনো এই পক্ষ, কখনো ওই পক্ষের
হয়ে লড়াই করে, সাত ঘাটের
পানি খেয়ে ব্রিটেনে
ফিরে আসেন ১৮২০ সালে।
ফিরেই ঘোষণা করেন তিনি
এখন “পয়েস” নামক এক দেশের
মালিক যা তিনি পেয়েছেন
স্থানীয় এক রাজার থেকে।
প্রচুর সম্পদে পরিপূর্ণ এই
জায়গায় এখন প্রয়োজন শুদু
ইউরোপিয়ানদের বিনিয়োগ।
সেই সময় স্প্যানিশদের
আধিপত্যের কারনে সাউথ
আমেরিকায় ব্রিটিশ বনিকরা
বিশেষ সুবিধা করতে পারতো
না। সুতরাং তারা কেও এই
সুযোগ হাতছাড়া করতে
চাইলো না। জর্জ ম্যাকগ্রেগর
রীতিমতো “পয়েস” এর
দূতাবাস খুলে শেয়ার বেচা
শুরু করেন। এমনকি “পয়েস” এর
অবস্তান দেখাতে একটি ম্যাপ
ও তৈরি করেন। ২ বছরের ভিতর
২,০০,০০০ পাউন্ড জোগাড় করে
ফেলেন। পরবর্তীতে শেয়ার
এর লাভের বদলে তিনি
বিনিয়োগকারীদের “পয়েস”
এর জমি দিতে চান। শুরুতে
অনেকেই রাজি না হলেও
শেষ পর্যন্ত দুই জাহাজ ভর্তি
সেটেলাররা রওনা হয় “পয়েস”
এর উদ্দেশে। বুজতেই পারছেন
“পয়েস” নামক দেশের চিহ্ন ও
তারা খুজে পায়নি।
ইউরোপের অনেক দেশে এই
একি প্রতারনা করে
পরবর্তীতে ভেনেজুএলায়
পালিয়ে যান এবং
সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।
দ্বিতীয় যার নাম আসবে
তিনি হলেন ভিক্তর লাস্তিগ।
হাঙ্গেরিয়ান এই ভদ্রলোক
বিখ্যাত তার বিভিন্ন স্কিম
এর জন্য। তিনি এমন কি
শিকাগোর গডফাদার আল
কাপন কেও বোকা
বানিয়েছেন। তবে তিনি
বিখ্যাত হয়েছেন কারন
তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি
পারিসের আইফেল টাওয়ার
বিক্রি করেছেন। তাও একবার
নয়, দুই দুইবার। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের
পরে প্যারিস তখন ঘুরে
দাঁড়িয়েছে। নতুন নতুন
স্তাপনা তৈরি হচ্ছে। কন
আর্টিস্টদের জন্য সেটা ছিল
সুসময়। লাস্তিগ ভুয়া সরকারি
পরিচয়পত্র দেখিয়ে কিছু
লোহার ব্যবসায়ীর সাথে
মীটিং করলেন। তাদের
জানালেন সরকার আইফেল
টাওয়ার বিক্রি করবে কারন
তা শহরের অন্যান্য স্থাপনার
সাথে মিলে না। শুরুতে
আসলেই পরিকল্পনা ছিল
আইফেল টাওয়ার সরিয়ে
ফেলা হবে। লাস্তিগ সেই
পরিকল্পনার সুযোগটাই
নিলেন। দুইজন ব্যবসায়ী রাজি
ও হয়ে গেলেন। লাস্তিগ
তাদের বিক্রির খবরটা গোপন
রাখতে বললেন চুক্তি না
হওয়া পর্যন্ত। এমনকি তাদের
ঘুরিয়ে আনলেন লিমজিনে
করে। চুক্তি শেষ হওয়ার পর
বুজতেই পারছেন টাকা নিয়ে
চম্পট দেন লাস্তিগ। দুই
ব্যবসায়ীর কেও আর পরে
লজ্জায় পুলিসের কাছে
অভিযোগ করতে যায়নি।
আমেরিকান কন আর্টিস্টদের
ভিতরে সম্ভবত সব চেয়ে
বেশী বিখ্যাত জর্জ সি
পার্কার। তার জন্ম ১৮৭০
সালে। তিনি বিক্রি করতেন
নিউইয়র্ক এর বিভিন্ন স্তাপনা।
তবে সবচেয়ে বেশী বিক্রি
করেছেন ব্রুকলিন ব্রিজ। আর
তার প্রিয় শিকার ছিল সেই
সময় আমেরিকায় নতুন আসা
অভিবাসীরা। তার
ক্রেতারা ব্রুকলিন ব্রিজে
টোল তোলার জন্য প্রায়
ব্যারিকেড দিতেন। পুলিস
আসার পর তারা বুজতে
পারতেন একজন কন আর্টিস্ট এর
শিকারে পরিনত হয়েছেন
তারা।
শেষ যার নামটি বলবো তিনি
হচ্ছেন মিথিলেশ কুমার
শ্রীবাস্তব যার জন্ম আমাদের
পাশের দেশ ভারতে। কন
আর্টিস্টদের মাঝে এই
লোককে একজন লিজেন্ড
হিসেবে মানা হয়। তিনি
সবচেয়ে বেশী পরিচিত
“নাটওয়ারলাল” নামে। এই
লোক তার পুরো জীবনে
বিক্রি করেছেন তাজ মহল,
লাল কেল্লা, রাষ্ট্রপতি ভবন,
এমন কি ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট
ভবন। সোজা কথায় ইন্দিয়ার
ঐতিহাসিক এবং সরকারি
গুরুত্বপূর্ণ স্তাপনা গুলো তিনি
বিক্রি করেছেন এমন কিছু
বিদেশীর কাছে যারা
ইন্ডিয়া সম্পরকে কিছুই
জানতো না। তাদের
অজ্ঞানতার সুযোগ নিতে ও
দেরি করেন নি এই কন
আর্টিস্ট। চিন্তা করুন এক
বিদেশী কোটিপতি লাখ
লাখ ডলার খরচ করে যখন
ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট কিনে
নিজের বাসা মনে করে
খুশিতে বাক বাকুম হয়ে
ভিতরে ঢুকতে যাবে তখন কি
হবে!
.jpg) টাইটানিক হারিয়ে যাওয়ার
গল্পঃ
টাইটানিকের গল্প তো
আপনারা জানেনই, কী
বিশালই না ছিল এই
টাইটানিক। প্রায় তিন-
তিনটা ফুটবল মাঠের সমান। শুধু
কী তাই? সেই কবেকার এই
জাহাজটিতে ছিল একটা
বিশাল সুইমিং পুল, যেখানে
গরম পানিরও বন্দোবস্ত ছিল।
ছিল আরাম আয়েশ আর বিলাস
এর সব ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে
যাকে বলে এক ভাসমান সুরম্য
প্রাসাদ। আর তাই দেখেন না,
টাইটানিক সিনেমায় যখন
জাহাজটিকে দেখে, মনেই
হয় না ওটা সেই ১৯১২ সালের
জাহাজ। বাজারে তো এমন
কথাও রটে গেল, স্বয়ং ঈশ্বরও
এই জাহাজকে ডোবাতে
পারবেন না, এমনই মজবুত এই
টাইটানিক!
এমন একটা জাহাজ, আর তাতে
রাজ্যের যতো বড়লোকরা
চড়বে না, তাই কি হয়?
রীতিমতো হুড়োহুড়ি করে
বিক্রি হল টাইটানিকের প্রথম
যাত্রার টিকিট। প্রথম
যাত্রার রুট ছিল ইংল্যান্ডের
সাউদাম্পটন শহর থেকে
আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর।
১৯১২ সালের ১০ এপ্রিল
সাউদাম্পটন থেকে রওয়ানা
হল তখনকার সবচাইতে বড় আর
সবচাইতে বিলাসী জাহাজ।
যারা জাহাজটির প্রথম
ভ্রমণে যাত্রী হতে পারলো,
তাদের তো খুশি আর ধরে না।
সারাদিনই যেন জাহাজে
পার্টি হচ্ছে, এমন অবস্থা।
এমনি করেই পার হয়ে গেল
কয়েকটি দিন।
১৪ এপ্রিল, রাত প্রায় ১২টা।
আটলান্টিক সাগরের বুকে
ভেসে যাচ্ছে টাইটানিক।
তখন টাইটানিক আমেরিকার
কাছাকাছি চলে এসেছে,
গ্র্যান্ড ব্যাংকস অফ
নিউফাউন্ডল্যান্ডে।
আবহাওয়া খুবই খারাপ; ভীষণ
ঠাণ্ডা আর জমাট বাঁধা
কুয়াশা। নিউফাউন্ডল্যান্ড
পার হয়ে যাওয়া
জাহাজগুলো এর মধ্যেই
এখানকার ভাসমান বরফ, মানে
আইসবার্গ সম্পর্কে সতর্ক করে
দিয়েছে টাইটানিককে।
কিন্তু টাইটানিকের
ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড জন স্মিথ
আর অন্যান্য ক্রুরা তো তাদের
এসব কথাকে পাত্তাই দেননি।
তাদের ভাবখানা এমন,
কোথাকার কোন বরফ নাকি
টাইটানিককে ডোবাবে!
টাইটানিক আগের মতোই ২১
নটিক্যাল মাইলে (২৪ মাইল)
চলতে লাগলো। ২১ নটিক্যাল
মাইলকে আবার কম ভেবেন
না; তখন টাইটানিক ছিল
অন্যতম দ্রুতগতির জাহাজ, আর
তার সর্বোচ্চ গতিই ছিল ২৪
নটিক্যাল মাইল।
ওদিকে জাহাজের সামনে
কোনো বাধা আছে কিনা
দেখার জন্য জাহাজের
ডেকে একটা উঁচু টাওয়ারের
মতো থাকে। সেখানে
পালা করে কয়েকজন চোখ
রাখে। তখন সেখানে ছিলেন
ফ্রেডরিক ফ্লিট। হঠাৎ তিনি
দেখলেন, কুয়াশার আড়াল
থেকে বের হয়ে এল এক
বিশাল আইসবার্গ। আইসবার্গ হল
সাগরের বুকে ভাসতে থাকা
বিশাল বিশাল সব বরফখণ্ড।
টাইটানিক হারিয়ে যাওয়ার
গল্পঃ
টাইটানিকের গল্প তো
আপনারা জানেনই, কী
বিশালই না ছিল এই
টাইটানিক। প্রায় তিন-
তিনটা ফুটবল মাঠের সমান। শুধু
কী তাই? সেই কবেকার এই
জাহাজটিতে ছিল একটা
বিশাল সুইমিং পুল, যেখানে
গরম পানিরও বন্দোবস্ত ছিল।
ছিল আরাম আয়েশ আর বিলাস
এর সব ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে
যাকে বলে এক ভাসমান সুরম্য
প্রাসাদ। আর তাই দেখেন না,
টাইটানিক সিনেমায় যখন
জাহাজটিকে দেখে, মনেই
হয় না ওটা সেই ১৯১২ সালের
জাহাজ। বাজারে তো এমন
কথাও রটে গেল, স্বয়ং ঈশ্বরও
এই জাহাজকে ডোবাতে
পারবেন না, এমনই মজবুত এই
টাইটানিক!
এমন একটা জাহাজ, আর তাতে
রাজ্যের যতো বড়লোকরা
চড়বে না, তাই কি হয়?
রীতিমতো হুড়োহুড়ি করে
বিক্রি হল টাইটানিকের প্রথম
যাত্রার টিকিট। প্রথম
যাত্রার রুট ছিল ইংল্যান্ডের
সাউদাম্পটন শহর থেকে
আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহর।
১৯১২ সালের ১০ এপ্রিল
সাউদাম্পটন থেকে রওয়ানা
হল তখনকার সবচাইতে বড় আর
সবচাইতে বিলাসী জাহাজ।
যারা জাহাজটির প্রথম
ভ্রমণে যাত্রী হতে পারলো,
তাদের তো খুশি আর ধরে না।
সারাদিনই যেন জাহাজে
পার্টি হচ্ছে, এমন অবস্থা।
এমনি করেই পার হয়ে গেল
কয়েকটি দিন।
১৪ এপ্রিল, রাত প্রায় ১২টা।
আটলান্টিক সাগরের বুকে
ভেসে যাচ্ছে টাইটানিক।
তখন টাইটানিক আমেরিকার
কাছাকাছি চলে এসেছে,
গ্র্যান্ড ব্যাংকস অফ
নিউফাউন্ডল্যান্ডে।
আবহাওয়া খুবই খারাপ; ভীষণ
ঠাণ্ডা আর জমাট বাঁধা
কুয়াশা। নিউফাউন্ডল্যান্ড
পার হয়ে যাওয়া
জাহাজগুলো এর মধ্যেই
এখানকার ভাসমান বরফ, মানে
আইসবার্গ সম্পর্কে সতর্ক করে
দিয়েছে টাইটানিককে।
কিন্তু টাইটানিকের
ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড জন স্মিথ
আর অন্যান্য ক্রুরা তো তাদের
এসব কথাকে পাত্তাই দেননি।
তাদের ভাবখানা এমন,
কোথাকার কোন বরফ নাকি
টাইটানিককে ডোবাবে!
টাইটানিক আগের মতোই ২১
নটিক্যাল মাইলে (২৪ মাইল)
চলতে লাগলো। ২১ নটিক্যাল
মাইলকে আবার কম ভেবেন
না; তখন টাইটানিক ছিল
অন্যতম দ্রুতগতির জাহাজ, আর
তার সর্বোচ্চ গতিই ছিল ২৪
নটিক্যাল মাইল।
ওদিকে জাহাজের সামনে
কোনো বাধা আছে কিনা
দেখার জন্য জাহাজের
ডেকে একটা উঁচু টাওয়ারের
মতো থাকে। সেখানে
পালা করে কয়েকজন চোখ
রাখে। তখন সেখানে ছিলেন
ফ্রেডরিক ফ্লিট। হঠাৎ তিনি
দেখলেন, কুয়াশার আড়াল
থেকে বের হয়ে এল এক
বিশাল আইসবার্গ। আইসবার্গ হল
সাগরের বুকে ভাসতে থাকা
বিশাল বিশাল সব বরফখণ্ড।
 এগুলোর সবচেয়ে ভয়ংকর
ব্যাপার হলো, এগুলোর মাত্রই
আট ভাগের এক ভাগ পানির
উপরে থাকে। মানে, এর বড়ো
অংশটাই দেখা যায় না। আর
বরফের রংও তো কুয়াশার
মতোই সাদা, তাই ফ্লিটও
প্রথমে ওটাকে আলাদা করে
চিনতে পারেনি। যখন
দেখতে পেল, ততোক্ষণে
আইসবার্গটি অনেক কাছে
চলে এসেছে।
ফ্লিট তো আইসবার্গ দেখেই
খবর দিতে ছুটলো। ফার্স্ট
অফিসার উইলিয়াম মারডক
শুনেই জাহাজ পিছনের দিকে
চালাতে বললেন। আর মুখ
ঘুরিয়ে দিতে বললেন
অন্যদিকে। যাতে
কোনভাবেই বিশাল ওই
আইসবার্গটির সঙ্গে
টাইটানিকের সংঘর্ষ না হয়।
কিন্তু লাভ হলো না।
টাইটানিকের স্টারবোর্ডে
আইসবার্গ ধাক্কা খেল। আর
তাতে টাইটানিকের পানির
নিচে থাকা অংশে
অনেকগুলো গর্ত হলো। পানি
ঢুকতে লাগলো দৈত্যাকার
জাহাজের খোলের ভেতর।
কিছুক্ষণের মধ্যেই এটা
পরিস্কার হয়ে গেল, লোকজন
যে জাহাজকে ভাবছিল
কখনোই ডুববে না, সেই
জাহাজই ডুবে যাচ্ছে তার
প্রথম যাত্রাতেই। এবার
যাত্রীদের লাইফবোটে তুলে
পার করে দেওয়ার পালা।
কিন্তু কেউ তো এ নিয়ে
ভাবেই নি। লাইফবোট যা
আছে, তা দিয়ে বড়োজোর
মোট যাত্রীদের তিন ভাগের
এক ভাগকে বাঁচানো যাবে।
তখন এক বিশেষ নীতি অনুসরণ
করা হলো, শিশু এবং
নারীদেরকে প্রথমে
লাইফবোটে করে পাঠানো
হতে লাগলো।
এমনি করে কোনো রকমে
বিশাল টাইটানিকের মোটে
৩২ শতাংশ যাত্রীদের
বাঁচানো গেল। মাত্র ঘণ্টা
চারেকের মধ্যে ডুবে গেল
সুবিশাল টাইটানিক, ১৫
এপ্রিল রাত ২টায়।
টাইটানিকের সঙ্গে
আটলান্টিকে ডুবে গেল প্রায়
১৫ শ' মানুষ। মানুষের
ইতিহাসেই এরকম বড়ো দুর্ঘটনা
আর ঘটেছে কিনা সন্দেহ।
টাইটানিক তো ডুবে গেল
আটলান্টিকে, কিন্তু
আটলান্টিকের বুকে তার কী
হলো? কেউ কেউ বললো,
টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।
কেউ বললো, টুকরো টুকরো হবে
কেন, দু’ভাগ হয়ে পড়ে আছে।
কিন্তু যতো গভীরে আছে,
সেখান থেকে টাইটানিকের
ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব
নয়। উদ্ধার কেন, চিহ্নিত করাই
তো অসম্ভব। এমনি করেই
আড়ালে চলে গেল হোয়াইট
স্টার লাইন কোম্পানির
জাহাজটি।
টাইটানিক খুঁজে পাওয়ার
গল্পঃ
কিন্তু টাইটানিককে
বেশিদিন চোখের আড়ালে
থাকতে দিলেন না রবার্ট
বালার্ড। ফরাসি এই
বিজ্ঞানীর ছোটবেলা
থেকেই ইচ্ছে ছিল
টাইটানিককে খুঁজে বের
করবেন। বড়ো হয়ে তিনি সেই
কাজেই নামলেন। ১৯৮৫ সালে
তিনি জাহাজ নিয়ে ঘাঁটি
গাড়লেন গ্রেট ব্যাংকস অফ
নিউফাউন্ডল্যান্ডে,
যেখানে ডুবে গিয়েছিল
টাইটানিক। সঙ্গে নিলেন
নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি।
এগুলোর সবচেয়ে ভয়ংকর
ব্যাপার হলো, এগুলোর মাত্রই
আট ভাগের এক ভাগ পানির
উপরে থাকে। মানে, এর বড়ো
অংশটাই দেখা যায় না। আর
বরফের রংও তো কুয়াশার
মতোই সাদা, তাই ফ্লিটও
প্রথমে ওটাকে আলাদা করে
চিনতে পারেনি। যখন
দেখতে পেল, ততোক্ষণে
আইসবার্গটি অনেক কাছে
চলে এসেছে।
ফ্লিট তো আইসবার্গ দেখেই
খবর দিতে ছুটলো। ফার্স্ট
অফিসার উইলিয়াম মারডক
শুনেই জাহাজ পিছনের দিকে
চালাতে বললেন। আর মুখ
ঘুরিয়ে দিতে বললেন
অন্যদিকে। যাতে
কোনভাবেই বিশাল ওই
আইসবার্গটির সঙ্গে
টাইটানিকের সংঘর্ষ না হয়।
কিন্তু লাভ হলো না।
টাইটানিকের স্টারবোর্ডে
আইসবার্গ ধাক্কা খেল। আর
তাতে টাইটানিকের পানির
নিচে থাকা অংশে
অনেকগুলো গর্ত হলো। পানি
ঢুকতে লাগলো দৈত্যাকার
জাহাজের খোলের ভেতর।
কিছুক্ষণের মধ্যেই এটা
পরিস্কার হয়ে গেল, লোকজন
যে জাহাজকে ভাবছিল
কখনোই ডুববে না, সেই
জাহাজই ডুবে যাচ্ছে তার
প্রথম যাত্রাতেই। এবার
যাত্রীদের লাইফবোটে তুলে
পার করে দেওয়ার পালা।
কিন্তু কেউ তো এ নিয়ে
ভাবেই নি। লাইফবোট যা
আছে, তা দিয়ে বড়োজোর
মোট যাত্রীদের তিন ভাগের
এক ভাগকে বাঁচানো যাবে।
তখন এক বিশেষ নীতি অনুসরণ
করা হলো, শিশু এবং
নারীদেরকে প্রথমে
লাইফবোটে করে পাঠানো
হতে লাগলো।
এমনি করে কোনো রকমে
বিশাল টাইটানিকের মোটে
৩২ শতাংশ যাত্রীদের
বাঁচানো গেল। মাত্র ঘণ্টা
চারেকের মধ্যে ডুবে গেল
সুবিশাল টাইটানিক, ১৫
এপ্রিল রাত ২টায়।
টাইটানিকের সঙ্গে
আটলান্টিকে ডুবে গেল প্রায়
১৫ শ' মানুষ। মানুষের
ইতিহাসেই এরকম বড়ো দুর্ঘটনা
আর ঘটেছে কিনা সন্দেহ।
টাইটানিক তো ডুবে গেল
আটলান্টিকে, কিন্তু
আটলান্টিকের বুকে তার কী
হলো? কেউ কেউ বললো,
টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।
কেউ বললো, টুকরো টুকরো হবে
কেন, দু’ভাগ হয়ে পড়ে আছে।
কিন্তু যতো গভীরে আছে,
সেখান থেকে টাইটানিকের
ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করা সম্ভব
নয়। উদ্ধার কেন, চিহ্নিত করাই
তো অসম্ভব। এমনি করেই
আড়ালে চলে গেল হোয়াইট
স্টার লাইন কোম্পানির
জাহাজটি।
টাইটানিক খুঁজে পাওয়ার
গল্পঃ
কিন্তু টাইটানিককে
বেশিদিন চোখের আড়ালে
থাকতে দিলেন না রবার্ট
বালার্ড। ফরাসি এই
বিজ্ঞানীর ছোটবেলা
থেকেই ইচ্ছে ছিল
টাইটানিককে খুঁজে বের
করবেন। বড়ো হয়ে তিনি সেই
কাজেই নামলেন। ১৯৮৫ সালে
তিনি জাহাজ নিয়ে ঘাঁটি
গাড়লেন গ্রেট ব্যাংকস অফ
নিউফাউন্ডল্যান্ডে,
যেখানে ডুবে গিয়েছিল
টাইটানিক। সঙ্গে নিলেন
নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি।
 আর্গো নামের একটি
আন্ডারওয়াটার ক্র্যাফট
পাঠিয়ে দিলেন সাগরতলে।
আর্গো সাগরতলের দৃশ্য
ভিডিও করে নিয়ে আসতো।
কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল
না টাইটানিককে। হতাশ হয়ে
পড়লেন বালার্ড। এদিকে
টানা পরিশ্রমে তার শরীরও
দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটু
বিশ্রাম দরকার তার। কিন্তু
কীসের বিশ্রাম! যেই একটু
ঘুমুতে গেলেন, অমনি তার
ডাক পড়লো। আর্গোর
ভিডিওতে মেটাল অবজেক্ট
পাওয়া গেছে, যেগুলো শুধু
কোনো জাহাজ থেকেই
ভেসে আসা সম্ভব।
উত্তেজনায় যা ঘুম ছিল, সব
চলে গেল বালার্ডের। একটু
খোঁজাখুজির পর
জাহাজটিকে পাওয়া গেল।
হ্যাঁ, এটাই টাইটানিকের
দৈত্যাকৃতির ধ্বংসাবশেষ।
এবার আর্গোকে দিয়ে
নানা দিক দিয়ে
টাইটানিকের ছবি তুললেন
বালার্ড। দেখলেন
টাইটানিকের যাত্রীদের
নানা স্মৃতিচিহ্ন, বিছানা,
সুটকেস, কাপ, প্লেট, আর অসংখ্য
জুতো। যেন সাগরতলের এক
জাদুঘরের ভিডিও দেখছেন
তিনি।
কিন্তু সময় ফুরিয়ে এল। তাকেও
ফিরে যেতে হলো। তখনই ঠিক
করলেন, আবার আসবেন
টাইটানিকের কাছে। পরের
বছরই আবার এলেন বালার্ড।
এবার আরো প্রস্তুত হয়ে।
ছোট্ট একটা সাবমেরিনে
চড়ে এলেন বালার্ড। সাথে
নিয়ে এলেন সাগরতলে
ঘোরাঘুরি করতে পারে, এমন
একটি রোবটও; নাম তার
জেজে। বালার্ড অবশ্য ওকে
বলতেন, সুইমিং আইবল।
জেজের সাহায্যে তিনি
দেখলেন পুরো টাইটানিককে;
এর বিশাল সিঁড়িটা এখন
কেমন আছে, কেমন আছে ওর
জিম, চেয়ার, ঘর, সব।
বালার্ডের টাইটানিক
আবিষ্কার তো হলো, কিন্তু
তিনি জানতে চাইলেন,
কীভাবে ডুবে গেল
টাইটানিক। আর তা বোঝার
জন্য আবারো তিনি গেলেন
টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষে,
২০০৪ সালের জুন মাসে। এবার
গিয়ে কিন্তু তার মনই খারাপ
হয়ে গেল।
বালার্ড টাইটানিক
আবিষ্কার করার পর থেকেই
মানুষ সাবমেরিনে করে
সেখানে ঘুরতে যায়। এই
সাবমেরিনগুলো
টাইটানিকের যে সব জায়গায়
ল্যান্ড করে, সেসব জায়গাতে
দাগ তো পড়েছেই, অনেক
জায়গায় গর্তও হয়ে গেছে। আর
মানুষ জাহাজ থেকে প্রায় ৬
হাজার জিনিস নিয়ে
গেছে। এমনকি অনেকে নিয়ে
গেছে জাহাজের টুকরোও!
তখন থেকেই টাইটানিকের
ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের
দাবি ওঠে। আর এ বছর তো
ইউনেস্কো টাইটানিকের
ধ্বংসাবশেষকে
আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ড
হেরিটেজ সাইট হিসেবেই
ঘোষণা করে দিয়েছে।
আর্গো নামের একটি
আন্ডারওয়াটার ক্র্যাফট
পাঠিয়ে দিলেন সাগরতলে।
আর্গো সাগরতলের দৃশ্য
ভিডিও করে নিয়ে আসতো।
কিন্তু কিছুতেই পাওয়া গেল
না টাইটানিককে। হতাশ হয়ে
পড়লেন বালার্ড। এদিকে
টানা পরিশ্রমে তার শরীরও
দুর্বল হয়ে পড়েছে। একটু
বিশ্রাম দরকার তার। কিন্তু
কীসের বিশ্রাম! যেই একটু
ঘুমুতে গেলেন, অমনি তার
ডাক পড়লো। আর্গোর
ভিডিওতে মেটাল অবজেক্ট
পাওয়া গেছে, যেগুলো শুধু
কোনো জাহাজ থেকেই
ভেসে আসা সম্ভব।
উত্তেজনায় যা ঘুম ছিল, সব
চলে গেল বালার্ডের। একটু
খোঁজাখুজির পর
জাহাজটিকে পাওয়া গেল।
হ্যাঁ, এটাই টাইটানিকের
দৈত্যাকৃতির ধ্বংসাবশেষ।
এবার আর্গোকে দিয়ে
নানা দিক দিয়ে
টাইটানিকের ছবি তুললেন
বালার্ড। দেখলেন
টাইটানিকের যাত্রীদের
নানা স্মৃতিচিহ্ন, বিছানা,
সুটকেস, কাপ, প্লেট, আর অসংখ্য
জুতো। যেন সাগরতলের এক
জাদুঘরের ভিডিও দেখছেন
তিনি।
কিন্তু সময় ফুরিয়ে এল। তাকেও
ফিরে যেতে হলো। তখনই ঠিক
করলেন, আবার আসবেন
টাইটানিকের কাছে। পরের
বছরই আবার এলেন বালার্ড।
এবার আরো প্রস্তুত হয়ে।
ছোট্ট একটা সাবমেরিনে
চড়ে এলেন বালার্ড। সাথে
নিয়ে এলেন সাগরতলে
ঘোরাঘুরি করতে পারে, এমন
একটি রোবটও; নাম তার
জেজে। বালার্ড অবশ্য ওকে
বলতেন, সুইমিং আইবল।
জেজের সাহায্যে তিনি
দেখলেন পুরো টাইটানিককে;
এর বিশাল সিঁড়িটা এখন
কেমন আছে, কেমন আছে ওর
জিম, চেয়ার, ঘর, সব।
বালার্ডের টাইটানিক
আবিষ্কার তো হলো, কিন্তু
তিনি জানতে চাইলেন,
কীভাবে ডুবে গেল
টাইটানিক। আর তা বোঝার
জন্য আবারো তিনি গেলেন
টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষে,
২০০৪ সালের জুন মাসে। এবার
গিয়ে কিন্তু তার মনই খারাপ
হয়ে গেল।
বালার্ড টাইটানিক
আবিষ্কার করার পর থেকেই
মানুষ সাবমেরিনে করে
সেখানে ঘুরতে যায়। এই
সাবমেরিনগুলো
টাইটানিকের যে সব জায়গায়
ল্যান্ড করে, সেসব জায়গাতে
দাগ তো পড়েছেই, অনেক
জায়গায় গর্তও হয়ে গেছে। আর
মানুষ জাহাজ থেকে প্রায় ৬
হাজার জিনিস নিয়ে
গেছে। এমনকি অনেকে নিয়ে
গেছে জাহাজের টুকরোও!
তখন থেকেই টাইটানিকের
ধ্বংসাবশেষ সংরক্ষণের
দাবি ওঠে। আর এ বছর তো
ইউনেস্কো টাইটানিকের
ধ্বংসাবশেষকে
আন্ডারওয়াটার ওয়ার্ল্ড
হেরিটেজ সাইট হিসেবেই
ঘোষণা করে দিয়েছে।
.jpg) ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ,
আমাদের ভীষণ আনন্দের দিন।
সেদিন তো খুব আনন্দ করবে।
কিন্তু পরের দিন মনে করে
টাইটানিকের সাথে ডুবে
যাওয়া ১৫শ’ মানুষের কথাও
স্মরণ করবেন। ঠিক ঠিক করে
বললে ১৫১৪ জন।
১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখ,
আমাদের ভীষণ আনন্দের দিন।
সেদিন তো খুব আনন্দ করবে।
কিন্তু পরের দিন মনে করে
টাইটানিকের সাথে ডুবে
যাওয়া ১৫শ’ মানুষের কথাও
স্মরণ করবেন। ঠিক ঠিক করে
বললে ১৫১৪ জন।
 আজকাল হাতে হাতে
হ্যান্ডি ক্যাম আর
ডিজিটাল ক্যাম থাকলেও
কয়েক দশক আগেও ছিল তা
দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই
১৯৬৫ সালে কোডাকই প্রথম
কোম্পানী যা মার্কেটে
নিয়ে বিখ্যাত ৮মিমি
হ্যান্ডি ক্যাম। সাথে
সাথে সয়লাব হয়ে যায়
মানুষের ঘরে ঘরে।
পার্টিতে নিয়ে আসে
আলাদা মাত্রা। তবে এই
ক্যাম এখন শো কেস এ ই
বেশী শোভা পায়।।
বেটামেক্সঃ
আজকাল হাতে হাতে
হ্যান্ডি ক্যাম আর
ডিজিটাল ক্যাম থাকলেও
কয়েক দশক আগেও ছিল তা
দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেই
১৯৬৫ সালে কোডাকই প্রথম
কোম্পানী যা মার্কেটে
নিয়ে বিখ্যাত ৮মিমি
হ্যান্ডি ক্যাম। সাথে
সাথে সয়লাব হয়ে যায়
মানুষের ঘরে ঘরে।
পার্টিতে নিয়ে আসে
আলাদা মাত্রা। তবে এই
ক্যাম এখন শো কেস এ ই
বেশী শোভা পায়।।
বেটামেক্সঃ
 আপনারা নিশ্চই ভিসিআর
ডিভাইসের ভিএইচএস
ক্যাসেট এর সাথে সবাই
পরিচিত। বেটামেক্স
হচ্ছে সেই VHS এর ঠিক আগের
প্রযুক্তি। ১৯৭৫ সালে
সনি মার্কেটে এই
বেটামেক্স এনে রীতিমত
সাড়া ফেলে দেয়।
আপনারা নিশ্চই ভিসিআর
ডিভাইসের ভিএইচএস
ক্যাসেট এর সাথে সবাই
পরিচিত। বেটামেক্স
হচ্ছে সেই VHS এর ঠিক আগের
প্রযুক্তি। ১৯৭৫ সালে
সনি মার্কেটে এই
বেটামেক্স এনে রীতিমত
সাড়া ফেলে দেয়।
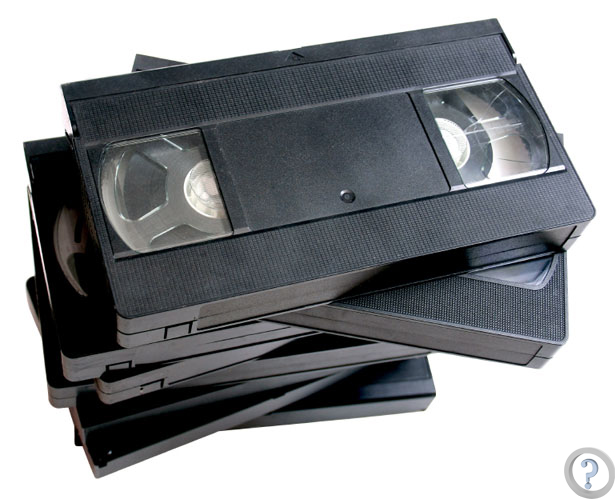 সনির বেটামেক্সের পরের
প্রযুক্তি হলেও এটি
মার্কেটে আনে JVC এবং
সে যে কি পরিমান
মার্কেটে দাপটের সাথে
রাজত্ব করেছে তা আমরা
ভালোই জানি এবং এর
বিলুপ্তিও আমরা নিজের
চোখেই অবলোকন করেছি।
লেজার ডিস্ক প্লেয়ারঃ
সনির বেটামেক্সের পরের
প্রযুক্তি হলেও এটি
মার্কেটে আনে JVC এবং
সে যে কি পরিমান
মার্কেটে দাপটের সাথে
রাজত্ব করেছে তা আমরা
ভালোই জানি এবং এর
বিলুপ্তিও আমরা নিজের
চোখেই অবলোকন করেছি।
লেজার ডিস্ক প্লেয়ারঃ
 আজকের ডিজিটাল
ভার্সেটাইল ডিস্ক (DVD)
মার্কেটে আসার আগে এই
লেজার ডিস্কই ছিল
উচ্চবিত্ত পরিবারের
বিনোদনের খোরাক। তবে DVD
মার্কেটে আসার পরে এর
করুনাবস্থা হয়।
ফোনোগ্রাফঃ
আজকের ডিজিটাল
ভার্সেটাইল ডিস্ক (DVD)
মার্কেটে আসার আগে এই
লেজার ডিস্কই ছিল
উচ্চবিত্ত পরিবারের
বিনোদনের খোরাক। তবে DVD
মার্কেটে আসার পরে এর
করুনাবস্থা হয়।
ফোনোগ্রাফঃ
 নতুন করে পরিচয় করিয়ে
দেয়ার মনে হয় প্রয়োজন নাই।
অনেকে গ্রামোফোন
নামেও চেনেন। ১৮৭৭ সালে
টমাস এডিসনের
জুগান্তকারী এই
আবিস্কারের মোহ থেকে
শত বছরেও মানুষের মুখ
ফেরাতে পারি নাই অন্য
কোন ডিভাইস। এখনও
শৌখিনেরা ড্রয়িং রুমে
গ্রামোফোন শুনে
নষ্টালজিক হয়।
TURNTABLES:
নতুন করে পরিচয় করিয়ে
দেয়ার মনে হয় প্রয়োজন নাই।
অনেকে গ্রামোফোন
নামেও চেনেন। ১৮৭৭ সালে
টমাস এডিসনের
জুগান্তকারী এই
আবিস্কারের মোহ থেকে
শত বছরেও মানুষের মুখ
ফেরাতে পারি নাই অন্য
কোন ডিভাইস। এখনও
শৌখিনেরা ড্রয়িং রুমে
গ্রামোফোন শুনে
নষ্টালজিক হয়।
TURNTABLES:
 আমাদের দেশে সরাসরি এই
জিনিসের ব্যবহার ছিল বলে
আমার জানা নেই। তবে এই
জিনিসই এখন আমাদের
দেশের DJ পার্টি এবং
রেকর্ডিং স্টুডিওতে
ব্যবহার করা হয়।
HM Radio:
আমাদের দেশে সরাসরি এই
জিনিসের ব্যবহার ছিল বলে
আমার জানা নেই। তবে এই
জিনিসই এখন আমাদের
দেশের DJ পার্টি এবং
রেকর্ডিং স্টুডিওতে
ব্যবহার করা হয়।
HM Radio:
 বিংশ শতাব্দীতে এই
কালচার স্টার্ট হলেও
জরিপে দেখা যায় এখনও ৬
মিলিয়ন লোক এই
প্রযুক্তির সাথে
প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষো
ভাবে সংযুক্ত। এই
প্রযুক্তির সাহায্যে
রেডিও অপারেটররা
শর্টওয়েভ রেডিও
কমিউনিকেশানে
কানেক্টেড থাকে। এ
পর্যন্ত হলিউডের বিভিন্ন
বিগ বাজেটে র মুভিতেও
মাঝে মাঝে এই ডিভাইস
ফিচারড হয়েছে।
REEL TO REEL:
বিংশ শতাব্দীতে এই
কালচার স্টার্ট হলেও
জরিপে দেখা যায় এখনও ৬
মিলিয়ন লোক এই
প্রযুক্তির সাথে
প্রতক্ষ্য ও পরোক্ষো
ভাবে সংযুক্ত। এই
প্রযুক্তির সাহায্যে
রেডিও অপারেটররা
শর্টওয়েভ রেডিও
কমিউনিকেশানে
কানেক্টেড থাকে। এ
পর্যন্ত হলিউডের বিভিন্ন
বিগ বাজেটে র মুভিতেও
মাঝে মাঝে এই ডিভাইস
ফিচারড হয়েছে।
REEL TO REEL:
 ক্যাসেট থেকে
ক্যাসেটে গান রেকর্ড
করার জন্যে সর্বপ্রথম এই
জন্ত্রটিই মার্কেটে
সাড়া জাগায়। জদিও এখন
কোথাও ব্যবহৃত হয়না। তবে
বছর খানেক আগে আমার
এলাকায় একটি রেকর্ডিং
সেন্টারে এই জিনিসের
কাজ কাম দেখার সুজোগ
হয়েছিল।
ট্রান্সিসটর রেডিওঃ
ক্যাসেট থেকে
ক্যাসেটে গান রেকর্ড
করার জন্যে সর্বপ্রথম এই
জন্ত্রটিই মার্কেটে
সাড়া জাগায়। জদিও এখন
কোথাও ব্যবহৃত হয়না। তবে
বছর খানেক আগে আমার
এলাকায় একটি রেকর্ডিং
সেন্টারে এই জিনিসের
কাজ কাম দেখার সুজোগ
হয়েছিল।
ট্রান্সিসটর রেডিওঃ
 এখনও গ্রামে আমাদের
অনেক ময় মুরুব্বী আছেন
যারা রেডিওকে
ট্রান্সিসটর নামেই
ডাকেন। অনেকেই হয়ত অবাক
হয় রেডিও কেন ট্রান্সিসটর
বলা হয়? এটা হয়েছে মূলত
তারা যে রেডিওতে
বিনোদনের সকল খোরাক
পেয়ে থাকতেন সেটিই ছিল
তখনকার মূল্যবান
ট্রান্সিসটার রেডিও।
ক্যাসেট টেপঃ
এখনও গ্রামে আমাদের
অনেক ময় মুরুব্বী আছেন
যারা রেডিওকে
ট্রান্সিসটর নামেই
ডাকেন। অনেকেই হয়ত অবাক
হয় রেডিও কেন ট্রান্সিসটর
বলা হয়? এটা হয়েছে মূলত
তারা যে রেডিওতে
বিনোদনের সকল খোরাক
পেয়ে থাকতেন সেটিই ছিল
তখনকার মূল্যবান
ট্রান্সিসটার রেডিও।
ক্যাসেট টেপঃ
 একটু আগে যে রিল টু রিল
যন্ত্রটি দেখিয়েছিলাম,
সেটিতে মূলত এই ধরনের
ক্যাসেটই রেকর্ড করা হত।
আর এর ব্যাপারে নতুন করে
বলার কিছু নেই। এমন কোন
টিউনার হয়ত খুজে পাওয়া
যাবে না যে কি না এই টেপ
একবার ভেঙ্গে এর নাড়ী
নক্ষত্র পরীক্ষা করে নাই।
বুম বক্সঃ
একটু আগে যে রিল টু রিল
যন্ত্রটি দেখিয়েছিলাম,
সেটিতে মূলত এই ধরনের
ক্যাসেটই রেকর্ড করা হত।
আর এর ব্যাপারে নতুন করে
বলার কিছু নেই। এমন কোন
টিউনার হয়ত খুজে পাওয়া
যাবে না যে কি না এই টেপ
একবার ভেঙ্গে এর নাড়ী
নক্ষত্র পরীক্ষা করে নাই।
বুম বক্সঃ
 ক্যাসেট টেপ বাজানোর
যে যন্ত্র, যেটা আমাদের
কাছে ক্যাসেট প্লেয়ার
নামে পরিচিত তা মূলত বুম
বক্স নামেই মার্কেটে
লিলিজ হয় ১৯৭০ সনে। শুরুর
দিকে খুবই ভারী ভারী হত
এগুলো। তবে মজার কথা
হচ্ছে সাইজ আর ওজন কমতে
কমতে এখন মার্কেট থেকেই
ভ্যানিশ হয়ে গেছে এই
জিনিস।
টেলিগ্রাফঃ
ক্যাসেট টেপ বাজানোর
যে যন্ত্র, যেটা আমাদের
কাছে ক্যাসেট প্লেয়ার
নামে পরিচিত তা মূলত বুম
বক্স নামেই মার্কেটে
লিলিজ হয় ১৯৭০ সনে। শুরুর
দিকে খুবই ভারী ভারী হত
এগুলো। তবে মজার কথা
হচ্ছে সাইজ আর ওজন কমতে
কমতে এখন মার্কেট থেকেই
ভ্যানিশ হয়ে গেছে এই
জিনিস।
টেলিগ্রাফঃ
 আজকের টেলেক্স অথবা
ফ্যাক্স ম্যাশিনের
পথিকৃতই ছিল এই
টেলিগ্রাফ যন্ত্র।
মিলিটারি, শিপিং
অপারেটর এবং সাধারন
মানুষের দ্রত
যোগাযোগের ক্ষেত্রে
সেই আমলে এটাই ছিল
অন্ধের যষ্টি। তবে আজকাল
এর দেখা মেলাই ভার।
,
,
,
আজকের টেলেক্স অথবা
ফ্যাক্স ম্যাশিনের
পথিকৃতই ছিল এই
টেলিগ্রাফ যন্ত্র।
মিলিটারি, শিপিং
অপারেটর এবং সাধারন
মানুষের দ্রত
যোগাযোগের ক্ষেত্রে
সেই আমলে এটাই ছিল
অন্ধের যষ্টি। তবে আজকাল
এর দেখা মেলাই ভার।
,
,
,
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg>)